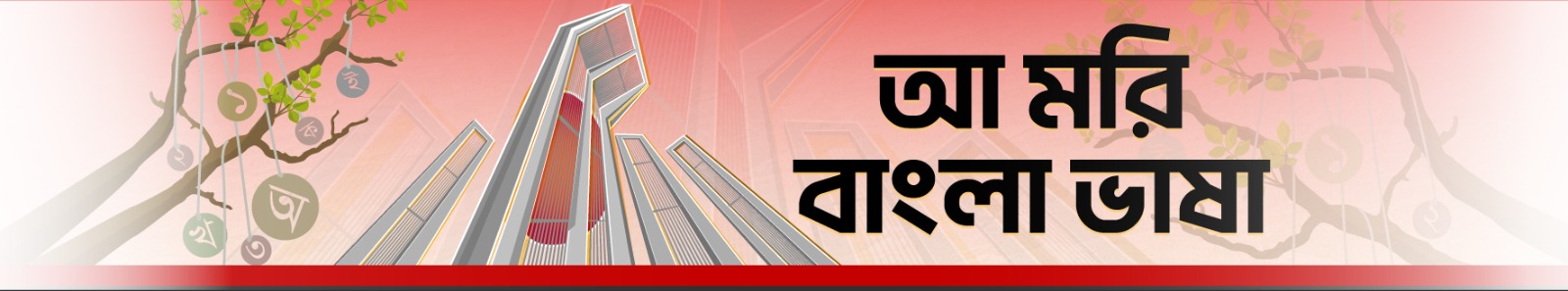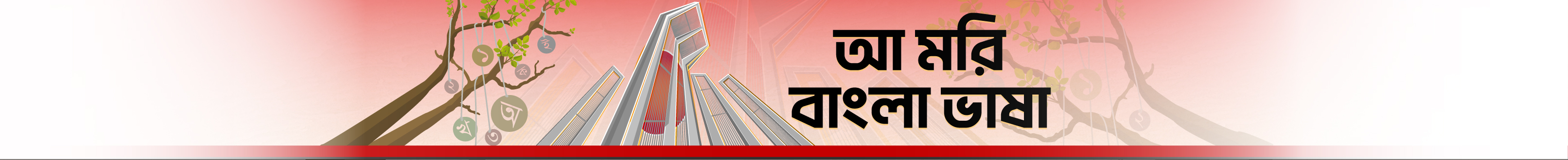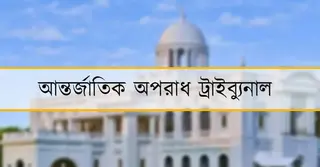রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে জুলাই থেকে মার্চ পর্যন্ত তৈরি পোশাক খাত থেকে বাংলাদেশ আয় করেছে ৩০.২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ১০.৮৪ শতাংশ বেশি।
তবে এই উন্নয়নের পেছনে রয়েছে একটি অন্ধকার দিক। উৎপাদন বাড়ছে, সাথে বাড়ছে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার—ফলে কমছে প্রাকৃতিক সম্পদ, আর বাড়ছে বৈশ্বিক তাপমাত্রা। তৈরি পোশাক খাত একাই দেশের মোট গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের ১৫.৪ শতাংশের জন্য দায়ী।
জাতিসংঘের জলবায়ু চুক্তি অনুযায়ী, বাংলাদেশকে ২০৩০ সালের মধ্যে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ নির্গমন কমাতে হবে। নইলে এই খাত আন্তর্জাতিক বাজারে টেকসই সংক্রান্ত নীতি ও বিধিনিষেধের মুখে পড়বে।
একদিকে টেকসই জ্বালানির দাবি, অন্যদিকে নিত্যনতুন প্রযুক্তি। অটোমেশনে উৎপাদনশীলতা বাড়লেও, শ্রমিকদের জ্ঞান ও দক্ষতা কী সেই হারে বাড়ছে?
গার্মেন্টস শ্রমিকদের মধ্যে একজন বলেন, 'সরকারের কাছে একটা অনুরোধ এটা যদি না থাকে কখনও, তখন যেন এমন একটা পরিস্থিতি করে দেয় যেটা করে আমরা সহজভাবে চলতে পারবো।'
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশে জাস্ট ট্রানজিশন বা ন্যায্য জ্বালানি রূপান্তরের পথে রয়েছে বড় কিছু বাধা। যেমন- নীতিগত অস্পষ্টতা, অর্থায়নের সংকট, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ঘাটতি।
ইএইএফএর প্রধান জ্বালানি বিশ্লেষক শফিকুল আলম বলেন, 'নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি দুটোকে যদি করি, তাহলে আমাদের এভারেজ বিদ্যুতের খরচ এবং জ্বালানির খরচ কমে যাবে। অর্থাৎ প্রফিট মার্জিন এখন যেটা থাকছে সেটা আরও বাড়বে। নতুন যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি পলিসি সরকার তৈরি করছে সেখানে এই ডিউটিগুলো শুল্কে অব্যাহতি দেয়ার কথা বলা আছে। সেটা যদি করা হয় তাহলে এই ট্রানজেকশনটা দ্রুত হবে।'
বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে অর্থায়ন, নীতিগত সহায়তা এবং কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে।
সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক মো. শামসুদ্দোহা বলেন, 'এমপ্লয়মেন্টটা হতে হবে, তাদের যে স্কিল আছে সেটাকে আপস্কেল করা, নতুন কিছু না। নতুন কিছু করলে সেটা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এবং তাদের যে শিক্ষার লেভেল আছে সেটা কনসিডার করে।'
পোশাকশিল্পে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষারও প্রশ্ন। তাই এই রূপান্তরে শ্রমিকদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়ার দাবি শ্রমিক সংগঠনগুলোর।
গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরামের সভাপতি মোশরেফা মিশু বলেন, 'ট্রানজেকশনের যে ব্যাপারগুলো এগুলো জানা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। মানে তারা আসলে জানে না এই ব্যাপারে। তাদের যেন একটা অলটারনেটিভ কাজের ব্যবস্থা করে দেন, এটা না করলে হঠাৎ করেই একদিন শ্রমিক এসে দেখবে তার মেশিন আর নেই এখানে, সে আর কাজ করতে পারছে না। এরকম একটা পরিস্থিতি যেন না হয়।'
পোশাক শিল্প মালিকরা বলছেন, জলবায়ু সহনশীল কর্মসংস্থান তৈরির জন্য মালিকদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে হবে। নবায়নযোগ্য প্রযুক্তি আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাস করারও আহ্বান জানান তারা।
বিকেএমইএ'র নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান বলেন, 'আমাদের সেক্টরেই তাকে অন্য কোথায় প্লেসমেন্ট করা যায়, তাদের মাল্টি-স্কিল অপারেশন শিখানো। আমাদের যখন একটা জায়গাতে লোক কম লাগে তখন এটার প্রোডাক্টিভিটি বাড়ার কারণে আমার কিন্তু আরেকটা কর্মসংস্থান আমার ফ্যাক্টরির মধ্যেই সৃষ্টি হয়। সে জায়গাগুলোতে তাদের মাল্টি-স্কিল শেখানোর জন্য আমরা অলরেডি একটা প্রজেক্ট চালু করেছি।'
নীতি সংশ্লিষ্টরা বলছেন, যেকোনো রূপান্তরে সমন্বয়হীনতার কারণে একপক্ষ সব সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে কীভাবে তাদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা যায় তা নিয়ে নীতি পরিকল্পনায় কাজ করছে অন্তর্বর্তী সরকার।
শ্রম সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'পরিবেশের ক্ষেত্রে, শিল্পের ক্ষেত্রে কীভাবে ট্রান্সফার করা যায় সেটা হয়েছে। কিন্তু তার কারণে শ্রমের ক্ষেত্রে যে প্রভাবটা এটা চিহ্নিত হয়নি। রূপান্তরিত জ্বালানির জন্য যে প্রযুক্তিগত বিকাশটা সেখানে যেন প্রশিক্ষিত হয় শ্রমিক। আমরা আমদানি করবো আর এখানে স্ক্রু-ড্রাইভার লাগাবো, রকম যেন না হয়। আমরা সবচেয়ে বেশি জোড় দিচ্ছি যে, ন্যায্য রূপান্তরের জন্য কী কী দরকার। এবং তার জন্য শিল্পকে এবং শ্রমিককে কীভাবে প্রস্তুত হওয়া দরকার। আর যারা এই পলিসিগুলো করছে তাদের মধ্যে সমন্বয় করা।'
বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, টেকসই বিনিয়োগ, গ্রিন ফান্ডের কার্যকর ব্যবহার এবং অংশীদারিত্বমূলক নীতির মাধ্যমেই সম্ভব হবে এই জ্বালানি রূপান্তর।